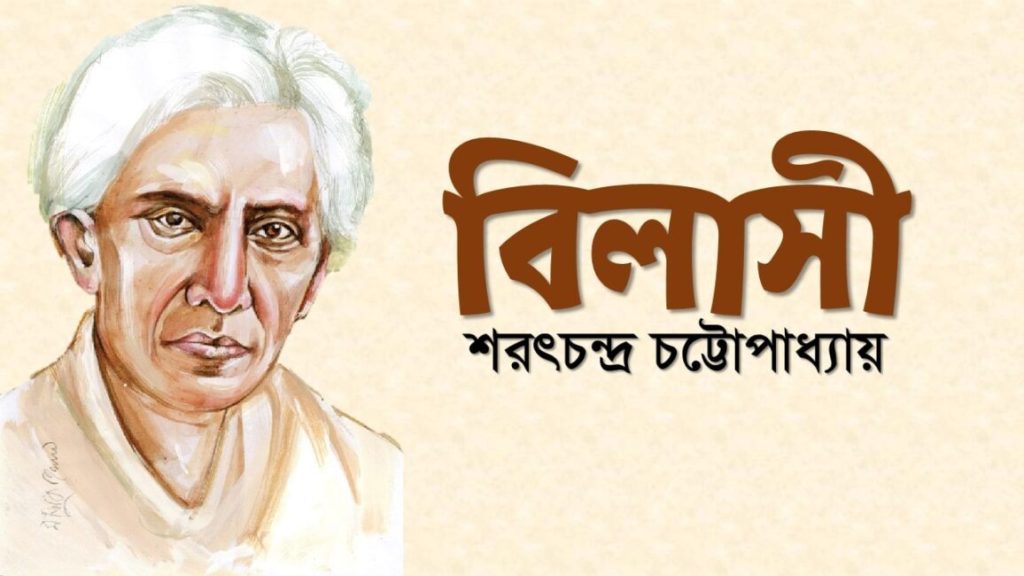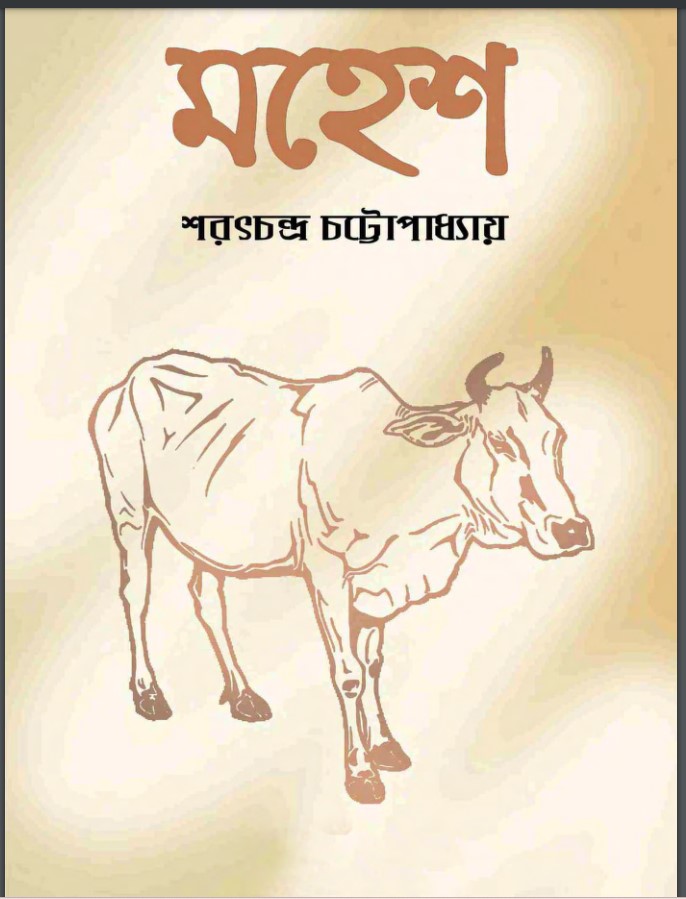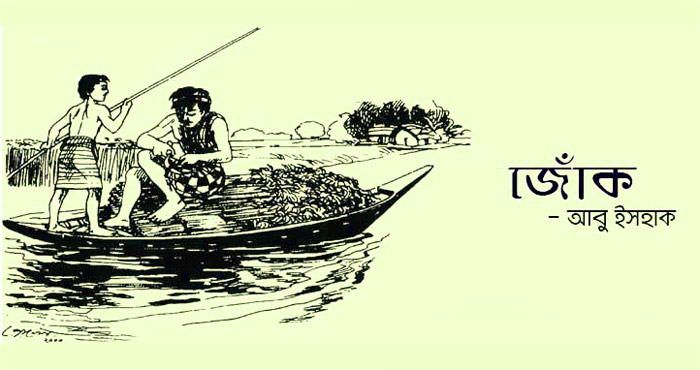আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অবাধ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে বৈধ অস্ত্র ব্যবহারে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে লাইসেন্স করা আগ্নেয়াস্ত্র নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে থানায় জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জারি করা নির্দেশনা অনুযায়ী লাইসেন্সধারীদের সব বৈধ আগ্নেয়াস্ত্র আগামী ৩১ জানুয়ারির মধ্যে সংশ্লিষ্ট থানায় জমা দিতে হবে। এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে নির্বাচনের আগে সম্ভাব্য সহিংসতা ও ভয়ভীতি রোধের অংশ হিসেবে।
রবিবার (১৮ জানুয়ারি) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা প্রজ্ঞাপনে জানানো হয় নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি দেশজুড়ে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এ সময়কে সামনে রেখে নিরাপত্তা ঝুঁকি কমাতে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়েছে ঘোষিত তফসিল অনুসরণে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্সধারীদের আগ্নেয়াস্ত্র বহন ও প্রদর্শন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ থাকবে। এই নিষেধাজ্ঞা নির্বাচন পরবর্তী সময় পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।
তবে রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও জাতীয় সংসদ সদস্য পদপ্রার্থীদের ক্ষেত্রে নির্ধারিত নীতিমালা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত বৈধ অস্ত্র এই নির্দেশনার আওতার বাইরে থাকবে। নির্বাচন কমিশনে বৈধভাবে মনোনয়নপত্র দাখিল ও গৃহীত জাতীয় সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী এবং তাদের জন্য অনুমোদিত সশস্ত্র রিটেইনারদের ক্ষেত্রে অস্ত্র প্রদর্শন নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত এই নির্দেশনা প্রযোজ্য হবে না।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্পষ্ট করে জানিয়েছে নির্দেশনা অমান্য করলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ আদেশ কার্যকর করতে দেশের সব পুলিশ সুপারসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানান নির্বাচনের সময় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে আগ্নেয়াস্ত্র জমা ও বহনে নিষেধাজ্ঞা একটি নিয়মিত ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে সহিংসতা ও আতঙ্কের ঝুঁকি অনেকটাই কমবে বলে আশা করা হচ্ছে।
নির্বাচনী নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে ভোটের পরিবেশ আরও শান্তিপূর্ণ রাখা সম্ভব হবে। তবে তারা মাঠপর্যায়ে নজরদারি ও তদারকি আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।